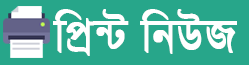

সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। তবে এই সংবিধান কিন্তু নিজে আমাদের বলতে পারে না যে আমাদের সেটা মানতে হবে। আমরা সেটা মানি কারণ, সেই বিষয়ে দেশের মানুষের একটা মৌন সম্মতি থাকে। ঠিক তেমনই, যখন একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়ে সরকারের পতন হয়, তখন সেই অভ্যুত্থান নিজেই একটা আইনি ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়। কারণ, তার প্রতি নাগরিকদের মৌন সম্মতি থেকে। এমনকি তরবারির জোরে এলেও একসময় নাগরিকেরা মেনে নিলে সেটাই সর্বোচ্চ আইনি ভিত্তি পায়।
আইনের চিন্তাভাবনার ভেতরও (অস্ট্রিয়ান-আমেরিকার জুরিষ্ট ও আইন বিশারদ হান্স কেলসনের ‘পিউর থিওরি অব ল’ বা গ্রুন্ডনর্ম) আইনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে সাধারণের বৈধতার ভাবনা স্বীকৃত। সরকার পতনের পর নতুন সাংবিধানিক কাঠামো সৃষ্টির বৈধতাকেও এই তত্ত্ব স্বীকৃতি দেয়। ব্রিটিশ আইন তাত্ত্বিক এইচ এল এ হার্টের ‘রুল অব রিকগনিশন’—আরও বলে যে রাষ্ট্রের সব অঙ্গের প্রতিনিধিরা যদি কোনো শাসককে মেনে নেয়, তবে সেই শাসন বৈধ। তার মানে, রাষ্ট্রের সব অঙ্গের নিয়ন্ত্রণ যে শক্তি নিতে পারবে, সেই শক্তিই বৈধ।
এই দুই ধারণা ধর্তব্যে নিলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বৈধতা পেতে সংবিধানের প্রয়োজন ছিল না। তারা জন-আন্দোলন থেকে তৈরি বলে সরকার হিসেবে তারা স্বয়ম্ভূ। যদি তারা সংবিধানের ১০৬ ধারার মাধ্যমে সাংবিধানিক পরম্পরা বজায় রাখতে চেষ্টা করে থাকে, তবে সেটা ছিল তাদের মর্জি। সেটা করার কোনো বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল না। হাইকোর্টের নির্দেশনা নয়, আইনের মৌলিক ভিত্তিবলেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তখন যেমন বৈধ ছিল, এখনো বৈধ।
শেখ সাহেবকে হত্যা করার পর ফারুক বা রশিদরা ক্ষমতা নেননি কারণ, তাঁরা জানতেন, সামরিক বাহিনীর ওপর তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অতএব দেশের মানুষের সম্মতি পাওয়ার কোনো উপায় তাঁদের নেই। এই অবস্থায় তাঁদের দেশের মানুষের সম্মতি এবং সেনাবাহিনীর সম্মতি আদায় করতে খন্দকার মুশতাককে ক্ষমতায় বসাতে হয়। একই কারণে কর্নেল তাহেরের অভ্যুত্থানের পর বিদ্রোহীরা সক্রিয় থাকায়, উপসামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের সায়েমকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সামনে রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর জিয়া প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে যান এবং পরে সায়েমের অবসরের পর রাষ্ট্রপতি হতে তাঁর আর কোনো বাধা থাকে না।
জিয়াউর রহমানের বৈধতা নিয়ে যতটুকু প্রশ্ন বাকি থাকে, সেটাও সমাধান করেন সাজানো হ্যাঁ/ না ভোট দিয়ে। ইতিহাস নিশ্চয়ই সেই গণভোটকে জিয়ার বৈধতার উৎস বলে মনে করে না। তাঁকে আবার কেউ অবৈধও বলে না। অবৈধ না বলার কারণ, আমার মতে, ডকট্রিন অব নেসেসিটি নয়, বরং রুল অব রিকগনিশনের জন্য বলে না। ইতিহাসে ক্ষমতার পালাবদলের নাটকে সাংবিধানিক বৈধতা খুব কম অঙ্কেই ভূমিকা রাখে, বরং সংবিধানই দেখা যায় নাটকের নায়ককে অনুসরণ করে।
জুলাই অভ্যুত্থান সাংবিধানিক পথে হয়নি, সে জন্য তার সাংবিধানিক ভিত্তি খুঁজে বের করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অভ্যুত্থানকারীরা জানতেন যে সেনাবাহিনীর কিছু অংশও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তেমনি সেনাবাহিনীও জানত যে তাদের সমর্থনের গণভিত্তি খুবই দুর্বল। শক্তির এই ভারসাম্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সৃষ্টি। সৃষ্টির পর সাংবিধানিক প্রশ্নের বোঝাপড়ায় এবং সমাজের পণ্ডিতদের চাপে ১০৬-এর মাধ্যমে তাদের বৈধতার সিল দিতে বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। লক্ষণীয় যে সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরই বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা চাওয়া হয়েছে। আমার মতে, এই প্রক্রিয়া একাডেমিক কারণ, আওয়ামী দলদাস এবং উপদেষ্টারা নিজেরা ছাড়া তত দিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে দেশের মানুষের এবং প্রশাসনের নিরঙ্কুশ সমর্থন এসে গিয়েছিল।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ইচ্ছা করলে নতুন সংবিধান তৈরি করতে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তৈরি করতে পারত বা ইচ্ছা করলে সাংবিধানিক পরম্পরা রক্ষা করার একটা উপায় বের করতে পারত আবার কিছু না করে দুদিন পর নির্বাচন দেওয়ার ঘোষণাও দিতে পারত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যত দিন জনপরিসরে তাদের বৈধতা আছে, তত দিন তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তাদের কাজ যত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং বিশেষত রাষ্ট্রের সব অঙ্গের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ যত দুর্বল বলে প্রকাশ পাচ্ছে, ততই তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে। সে জন্যই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন এখন আমাদের সামনে।
এই সরকার এই দেশের নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষাকে বুঝে চলার চেষ্টা করছে এবং সেই লক্ষ্যেই তাদের কাজ সাজানোর চেষ্টা করছে। জন-অসন্তোষ থেকে বাঁচার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটা সাংবিধানিক পরম্পরায় নিজেদের যুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। জন-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার জন্যই তারা ঐক্য কমিশন সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিকভাবে সব রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে সংস্কারের প্রস্তাব তৈরি করেছে।
একই জন-আকাঙ্ক্ষাকে মাথায় রেখে বাস্তবায়নের পথও তারা খুঁজে নিতে পারে। সংস্কার প্রস্তাবের মতো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও গণতান্ত্রিকভাবে খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়া এখন চলমান। এই প্রক্রিয়ায় যদি ঐকমত্যে না পৌঁছাতে পারে, তবে তাদের বুঝতে হবে যে নেতৃত্ব মানে শুধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পালন করা নয়। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাদের যে দায়িত্ব দিয়েছে, তাতে অচলাবস্থা নিরসনের জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৈধতা তাদের আছে। শুধু খাস নিয়তের বিষয়ে আপস না করলেই হবে।
খাস নিয়ত নিয়ে ভাবলে বাস্তবায়নের সীমারেখাগুলো কী হবে, সেটা তারা নিজেরাই পেয়ে যাবে। ঐক্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব দেখলে কোন প্রস্তাব সর্বোত্তম, সেটা আরও পরিষ্কার হবে। তারা নিজের মনের ভেতর খুঁজলেই দেখবে যে রাষ্ট্রপতির প্রজ্ঞাপন দিয়ে সংবিধানের পরিবর্তন করলে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার হবে। গণভোট ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতির জন্য হুমকি হলেও তারা বুঝতে পারবে যে সেটা জন-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে যাবে। আবার দেখবেন, সংবিধানের ১০৬ ধারা ব্যবহার করে আপিল বিভাগ দিয়ে আগামী সংসদকে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে চাপ দেওয়ার চেষ্টার পক্ষেই ঐক্য কমিশনে সমর্থন বেশি। গণপরিষদ করে সংবিধান নতুন করে লেখার ঝুঁকি এই প্রস্তাবে নেই। সনদে লেখা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের সম্ভাবনা যেমন এই প্রস্তাবে বেশি, তেমনি নতুন সংসদ নির্বাহী দায়িত্ব নিয়ে দেশকে নিরাপদ করার বিষয়ও এই প্রস্তাবে সংযুক্ত।
ঐক্য কমিশনের সভায় এটা পরিষ্কার যে সভার পরিসমাপ্তিতে কমিশন কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবে না এবং তারা কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ রাখবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি তার বৈধতা এবং দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকে, তবে তাদেরই সেই প্রস্তাব থেকে একটা পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। দেশের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে দেশের মানুষ সেই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে।



